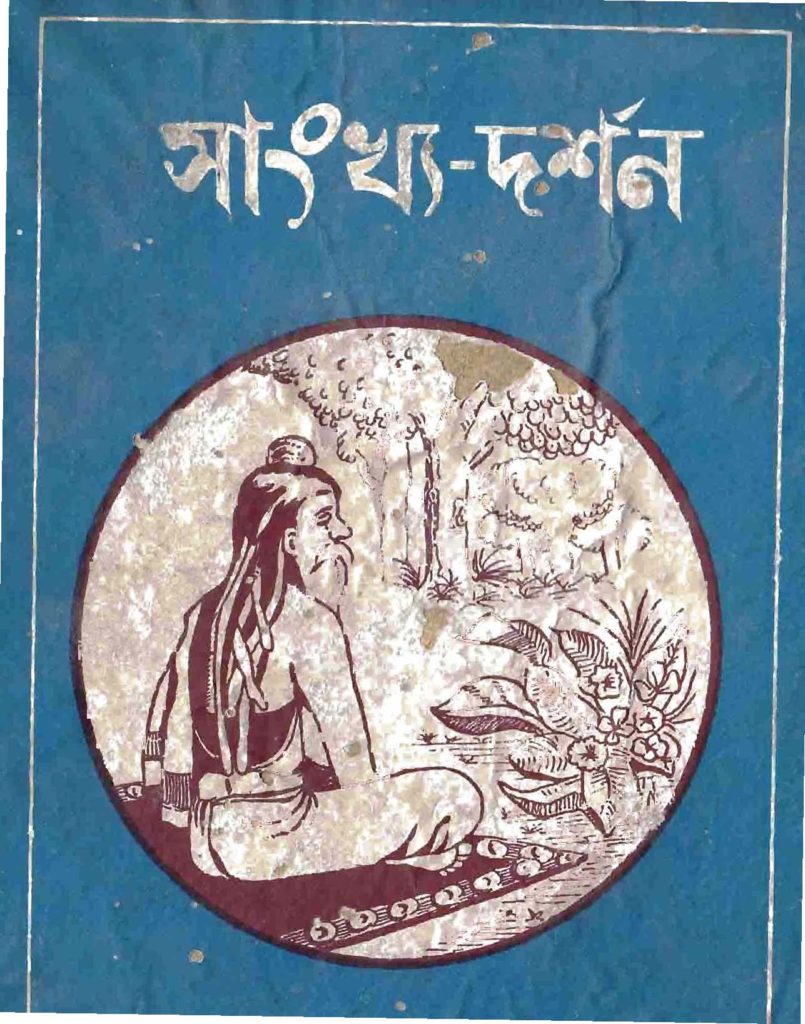ভুমিকাঃ
ভারতে ছয়টি আস্তিক দর্শন ও তিনটি নাস্তিক দর্শন আছে। যারা বেদকে প্রামাণ্য স্বীকার করে তারাই আস্তিক দর্শন আর বেদকে যারা ঐশ্বরিক বলে স্বীকার করেনা তাঁরা নাস্তিক। ছয়টি আস্তিক দর্শনকে একসাথে বলা হয় ষড় দর্শন।
আস্তিক দর্শন (ষড় দর্শন)
১/ মীমাংসা
২/ বেদান্ত
৩/ সাংখ্য
৪/ যোগ
৫/ বৈশেষিক
৬/ ন্যায়
নাস্তিক দর্শন
১/ বৌদ্ধ
২/ জৈন
৩/ চার্বাক
এটা খুব কৌতূহল উদ্দীপক যে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম দর্শনও নাস্তিক দর্শন হিসেবে পরিচিত শুধু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করার জন্য। বেদান্ত ও মীমাংসা ছাড়া অন্য সব আস্তিক দর্শন বেদ বা উপনিষদের ভাবনা ছাড়াই স্বাধীনভাবে স্বাধীন দার্শনিকদের চিন্তায় উদ্ভুত হয়েছে। যদিও এই দর্শনগুলোতে ধর্মভাব প্রবলভাবেই বর্তমান তবুও বাকি চারটি দর্শনকে বেদান্ত আর মীমাংসা বাদীদের প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছে। বেদান্তের আক্রমন সবচেয়ে তীব্র ছিল সাংখ্য দর্শনের উপরে। বাঙলার ভাবুকদের মধ্যে এবং বিশেষ করে নদীয়ায় সাংখ্য দর্শনের প্রভাব প্রবল তাই বাঙলার ভাবকে বুঝতে হলে সাংখ্য দর্শন সম্পর্কে একটা সাধারন ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।
সাংখ্য দর্শনের গ্রন্থ সমুহ ও রচয়িতা
সাংখ্য দর্শনের মৌলিক গ্রন্থ তিনটি। তত্ত্ব সমাস গ্রন্থ এটায় আছে ২২ টি সুত্র; ঈশ্বরকৃষ্ণের ৭০ টি কারিকা; আর “সাংখ্য প্রবচন সুত্র” নামের একটি বৃহৎ সুত্র গ্রন্থ। বিশেষজ্ঞরা সাংখ্য প্রবচন সুত্র গ্রন্থটিকে অর্বাচিন বলে অভিহিত করেন, এই গ্রন্থের তেমন কোন দার্শনিক মূল্য নাই। এই তিনটি গ্রন্থ ছাড়া দুইটি টিকা গ্রন্থ আছে একটি ৯ম শতাব্দীতে লেখা বাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্য কারিকর টিকা আর ১৬ শতাব্দীতে বাঙালি দার্শনিক বিজ্ঞান ভিক্ষুর সাংখ্য সুত্রের ভাষ্য। আমার ধারণা সাংখ্য দর্শন বাঙলায় উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে; বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য রচনাই এর একমাত্র কারণ নয় আরো কিছু কারণ আছে যার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক কপিল ঋষি। কপিল শব্দের অর্থ তামাটে। সাংখ্য দর্শনের আরো অন্যান্য দার্শনিকদের নাম হচ্ছে আসুরি, পঞ্চশিখ, সনন্দ। আসুরি শব্দটা “অসুর” থেকে আসতে পারে যা সাংখ্য দর্শনের অনার্য উৎপত্তিকে নির্দেশ করে। এছাড়াও বাঙালি হিন্দুদের তর্পণ বিধিতে সাংখ্য দার্শনিকদের তর্পণের ব্যবস্থা আছে যা বাঙালি ভিন্ন অন্য হিন্দু সম্প্রদায়ে নেই। যেমন,
“ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতন;
কপিলশ্চসুরিচৈব বোঢ়ঃ পঞ্চশিখস্তথা;
সর্বে তে তৃপ্তিমায়ান্ত মদ্দেত্তেনাম্বুনা সদা।”
সাংখ্য দর্শনের মুল কথাঃ
সাংখ্য দর্শনে ২৫ টি তত্ত্বের উপদেশ আছে। কী কী সেই তত্ত্ব? প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, ১১ টি ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ৫ টি ইন্দ্রিয়, এছাড়া ৫ টি কর্মেন্দ্রিয় যেমন বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ; এছাড়া মন আরেকটি ইন্দ্রিয়), ৫ টি তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) ও ৫টি মহাভুত (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী) এই হলো ২৪ টি তত্ত্ব আর বাকি ১ টা তত্ত্ব হচ্ছে “পুরুষ”। এই ২৫টি তত্ত্বের আবির্ভাব, পরস্পরের সন্মন্ধ এই সাংখ্য দর্শনের মুল প্রতিপাদ্য।
পুরুষ ছাড়া বাকি ২৪ তত্ত্বের মুল তত্ত্ব হচ্ছে “প্রকৃতি”। প্রকৃতির মধ্যেই জগতের সকল উপাদান। প্রকৃতি সত্ত্ব, তম ও রজ এই তিনটি গুনের সাম্যবস্থা। অর্থাৎ যখন এই তিনটি গুন কোন বিক্ষোভ সৃষ্টি না করে সমানভাবে অবস্থান করে তার নামই “প্রকৃতি”।
সত্ত্ব – স্থিরতা, সৌন্দর্য, ঔজ্জ্বল্য ও আনন্দ;
রজঃ – গতি, ক্রিয়াশীলতা, উচ্ছ্বাস ও যন্ত্রণা;
তমঃ – সমাপ্তি, কঠোরতা, ভার, ধ্বংস, ও আলস্য।
প্রকৃতি সাম্যবস্থায় নিষ্ক্রিয়, অচেতন ও জড়। পাশ্চাত্ত্য দর্শন মতে এটাই বস্তু জগত। প্রকৃতি পুরুষের সংস্পর্শে এসে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই পুরুষ হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের “ভাব” বা “চৈতন্য”। ভাবের সংস্পর্শে প্রকৃতির সাম্যবস্থা নষ্ট হয়, প্রকৃতি প্রান পায়। এই চৈতন্য বা ভাব বা পুরুষ যখন প্রকৃতিকে জানতে পারে তখন প্রকৃতি সংকুচিত হয়ে সরে যায় এবং চৈতন্য মুক্ত হয়। ভাবের দিক থেকে বস্তুকে দেখা বা পুরুষের দিক থেকে প্রকৃতিকে দেখা বা প্রকৃতির দিক থেকে পুরুষকে দেখার কারনেই সাধক যেই আশ্রয় ধারণ করে সেই আশ্রয়ের চোখে জগত কখনো পুরুষ হিসেবে আর কখনো প্রকৃতি হিসেবে দেখা দেয়। এটাই বস্তু ও ভাবের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে সাংখ্য দর্শন “লীলা” বলে।
সাংখ্য দর্শন মতে বস্তুর লোপ নাই, নতুন বস্তুর আবির্ভাব নাই; আছে শুধু বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তি। এটাই বস্তুর অবিনাশী তত্ত্ব। ল্যাভয়সিয়ের বস্তর অবস্থান্তর তত্ত্ব, জোসেফ প্রুস্তের ডেফিনিট প্রপোরশন আর ডালটনের পরমানু তত্ত্ব এই বস্তুর অবিনাশী তত্ত্বের উপরে দাড়িয়ে আছে।
ভারতবর্ষে যোগীদের অতীত ও অনাগতকে প্রত্যক্ষ করেন বলে কথিত ছিল। এই সম্ভাবনা এই অবিনাশী তত্ত্বেই লুকিয়ে আছে। দুধে দইয়ের সম্ভাবনা আছে; আর যে অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হয়েছে সেই অঙ্কুর একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই বস্তুর পরিনাম বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি যিনি জানেন তিনি অতীত ও অনাগতকে বর্তমানের মতো প্রত্যক্ষ করতে পারেন। কার্যে লীন কারণ ও কারণে অব্যক্ত কার্য দুটোকেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।
সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর নাই। কারণ জগত-প্রপঞ্চ ব্যাখ্যায় প্রকৃতি আর পুরুষই যথেষ্ট। তাই এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না, বেদের প্রামাণ্য মানলেও কেন বেদান্তবাদীদের আক্রমন সাংখ্য দর্শনকে সহ্য করতে হয়েছে। পুরুষ মুক্তি পায় সে যখন প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।
প্রকৃতি ও পুরুষের ধারনাঃ
প্রকৃতি ও পুরুষের ধারনাই পশ্চিমে বস্তু আর ভাব হিসেবে বিকশিত হয়েছে। ভাব ও বস্তুর ইউরপিয়ান দান্দিক সম্পর্ক ভারতবর্ষে “লীলা” বলে পরিচিত। এখানেই পশ্চিমের চিন্তার সাথে আমাদের মোকাবেলার শর্ত তৈরি হয়ে যায়। প্রকৃতি শব্দটা সংস্কৃত ব্যকরন অনুযায়ী স্ত্রীবাচক। প্রকৃতিকে তাই কোথাও লজ্জাশীলা বধু (কারিকা, ৬১) কোথাও নর্তকী (সুত্র ৩।৬৯) হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শন হলেও নারি আর পুরুষের প্রেম, অপ্রেম আর লীলা কাব্যেও রূপ পেয়েছে। পুরুষ-প্রকৃতির সম্পর্ককে নর-নারীর সনাতন সম্পর্কের রূপক হিসেবেই দেখা হয়েছে। দর্শন থেকে কাব্যের এমন মনোহর উত্তরণ পশ্চিমে হয়নি। আমরা অবশ্য কাব্য ধরে দর্শন ভুলে গেছি। রাঁধা আর কৃষ্ণ বাঙলার ভাব চর্চায় সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি আর পুরুষের প্রতীক। রাঁধা আর কৃষ্ণের প্রেম হচ্ছে লীলা যা প্রতিকায়িত করেছে বস্তু আর ভাবের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে।
সাংখ্য দর্শন বাঙলার ভাব ও হেগেলঃ
মুল সাংখ্য দর্শনে মোক্ষ অর্জন তখনই সম্ভব বলে বলা হয়েছে যখন পুরুষ ও প্রকৃতি পৃথক জ্ঞান হয়, সেই মুহুর্তে আত্মা জন্মান্তরের হাত থেকে মুক্ত হয়ে কৈবল্য বা মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ঠিক যেভাবে হেগেল চৈতন্য আর বস্তু জগতকে আলাদা জ্ঞান করে চৈতন্যকে আলাদা একটা বৈষয়িক সত্তা দিয়েছেন। বাঙলার ভাব মুল সাংখ্য দর্শন থেকে এইখানেই আলাদা। বাঙলার ভাব মার্ক্সের মতো বস্তু আর ভাবের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক অর্থাৎ “লীলা” কে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়েছে।