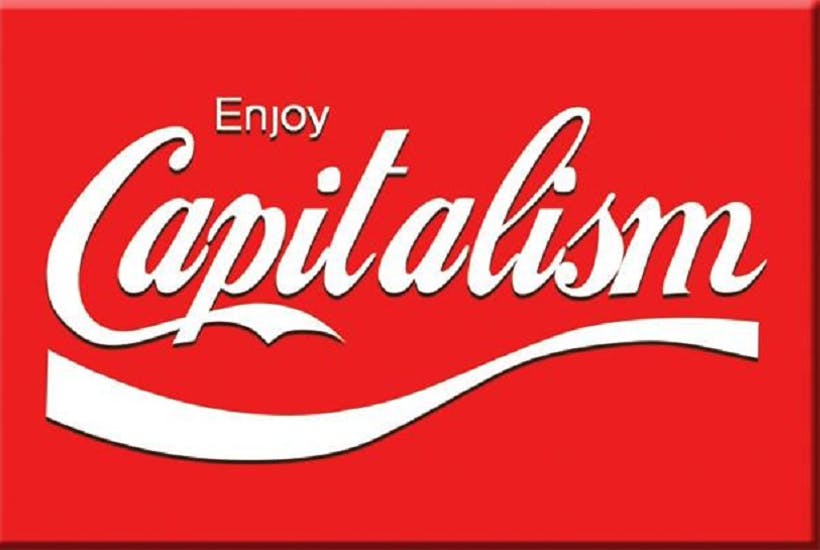ক্যাপিটালিজমের জন্ম হয়েছে ইংল্যাণ্ডে, কিন্তু তার আধ্যাত্মিক তীর্থ হচ্ছে আমেরিকা। ইংল্যাণ্ডে ক্যাপিটালিজমের উত্থানের সময়ে কৃষির সাথে যুক্ত অভিজাততন্ত্রের ক্ষমতা ও রাজনৈতিক শক্তির সাথে দীর্ঘমেয়াদে মরনপন লড়াই করতে হয়েছিলো উঠতি বুর্জোয়াদের। আর আমেরিকাতে ক্যাপিটালিজম প্রথম থেকেই ডমিন্যান্ট পলিটিক্যাল ফোর্স।
দাস শ্রমের উপরে দাঁড়ানো কৃষির উপর নির্ভরশীল আমেরিকার দক্ষিন অংশের উপরে যখন অগ্রসর আমেরিকার উত্তর অংশ জয়লাভ করলো, সেটা শুধু আমেরিকার স্বাধীনতার লড়াইয়ের বিজয়ই ছিলোনা। সেটা ছিল ক্যাপিটালিজমের বিজয়ও।
১৯ শতকের শেষ দিকে ইউরোপে যে ক্যাপিটালিজমের উদ্ভব হয়েছিলো, সেটার মুল চালিকাশক্তি ছিলো ক্যাপিটাল বা পুজির সাথে শ্রমের রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব। আমেরিকাতে যে সমস্ত এন্টি ক্যাপিটালিস্ট ফোর্স পরবর্তীতে তৈরি হয়েছে তা কখনোই ইউরোপের মতো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি।
ওয়ার্রকারদের অধিকার আমেরিকাতে প্রায় নেই বললেই চলে। মালিকের ইচ্ছাতেই বেশীরভাগ আমেরিকান শ্রমিককে ছাটাই করে দেয়া সম্ভব। অথচ, এই কাজটা ইউরোপ বা জাপানে করাটা অসম্ভব। আমেরিকায় ইউরোপের মতো সোশ্যাল সেফটি নেট নেই, সার্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেই, কাজ ইউরওপের চেয়ে বেশী করতে হয়, ইউরোপের চাইতে পেইড হলিডের সংখ্যা কম।
কিন্তু আমেরিকান ক্যাপিটালিজম ইউরোপের চাইতে অনেক বেশী ডাইনামিক। যেমন ধরেন বড় কর্পোরেটের সংখ্যা ইউরোপ আর আমেরিকাতে সমান। কিন্তু গত তিরিশ বছরে স্থাপিত হয়েছে এমন বড় কর্পোরেট ইউরোপে নেই। কিন্তু সাতটা বড় কর্পোরেটের মধ্যে একটা বড় কর্পোরেট আমেরিকান। এপল, আমাজান, ফেইসবুকের তুল্য বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইউরোপে নেই।
আমেরিকাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন অস্বাভাবিক। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রায় পুরোটাই যায় এক শতাংশ মানুষের কাছে। আমেরিকান মডেল কম প্রবৃদ্ধির বিনিয়োগ থেকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির বিনিয়োগে পুজি স্থানান্তরের একটা দারুন মডেল। কিন্তু পুজি স্থানান্তর করলেও, শ্রমশক্তিকে সে এক শিল্প থেকে আরেক শিল্পে সফলভাবে স্থানান্তর করতে পারেনা।
আমেরিকায় নির্বাচনী খরচের উপরে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ইন্টারেস্টিংলি যারা বেশী চাদা সংগ্রহ করতে পারে তারাই রাস্ট্রপতি নির্বাচনে জেতে। এর ফকে আর্থিক শক্তি খুব সহজেই রাজনৈতিক শক্তিতে রুপান্তরিত হয়ে যায়।
আবার চায়নাতে আরেক বৈশিষ্ট্যের ক্যাপিটালিজম তৈরি হয়েছে। চাইনিজ ক্যাপিটালিজমে যে ধরনের প্রবৃদ্ধি হয়েছে সেটা আগে কখনো ক্যাপিটালিজমের ইতিহাসে হয়নি।
ইউরোপে ক্যাপিটালিজমের উদ্ভবের সাথে সাথেই গনতন্ত্রের ধারণা স্ফুরিত হয়েছে। মনে করা হতো ক্যাপিটালিজমের জন্য গনতন্ত্র অপরিহার্য। অথচ এই ধারণাও টিকছেনা, অনেক স্বৈরতান্ত্রিক দেশেও ক্যাপিটালিজম ভালো ফাংশন করছে অথচ অবেক গনতান্ত্রিক দেশেও ক্যাপিটালিজম গড়েই উঠতে পারছেনা।
এইসব অভিজ্ঞতাই আমাদের জন্য জরুরী। কারণ আমাদের সামনে কোন তৈরি নিখুঁত মডেল নেই। আর পৃথিবীতে কোন একক ক্যাপিটালিজমের মডেল কেউ অনুসরণও করেনা। ক্যাপিটালিজম সেই অর্থে নির্দিষ্ট দেশে নির্দিস্ট সময়ের একটা বুদ্ধিবৃত্তিক নির্মান।
আমরা কি আমাদের ক্যাপিটালিজমের মডেল নিজেরা তৈরি করার হিম্মত রাখি? আসুন ভাবতে থাকি, এই নিয়ে ভাবার প্র্যাক্টিস করি।