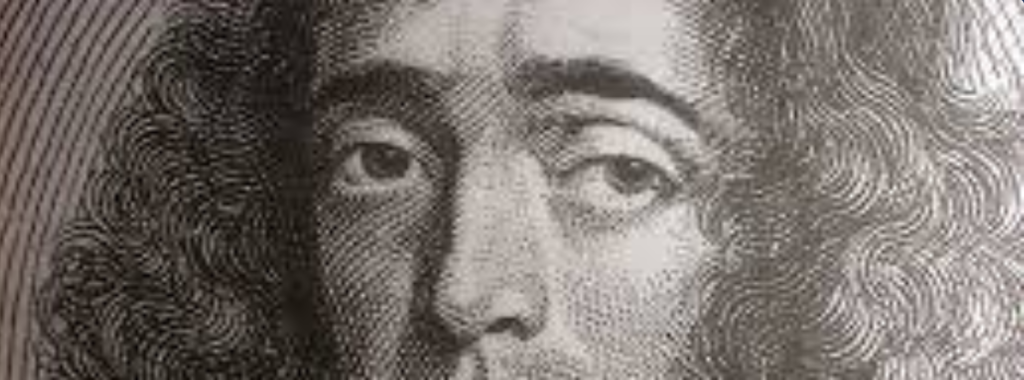স্পিনোজাকে গভীরভাবে বুঝতে হলে তাঁর মৌলিক অবদানকে শনাক্ত করতে হলে স্পিনোজার আগে ইউরোপের চিন্তার ইতিহাসটা বুঝে নিতে হবে। স্পিনোজার চিন্তা দাড়িয়ে আছে দেকার্তের চিন্তার বিপরীতে। দেকার্তই বস্তু এবং চিন্তার দ্বি বিভাগের দার্শনিক খুটি। দেকার্ত জগতের অস্তিত্বের প্রশ্নকেও যুক্ত করেছেন চিন্তাশীলতার সাথে। তিনি বলেছিলেন “আই থিঙ্ক দেয়ারফৌর এই অ্যাম।“ আমি চিন্তাশীল তাই আমি অস্তিত্তবান। জগতের উপর চিন্তার আধিপত্য মানে জগতকে চিন্তা দিয়ে নিয়ন্ত্রনে নেয়ার দার্শনিক ভিতটাও তৈরি করে দেয়া। এটাই পুঁজিবাদের দার্শনিক ভীত। এটাই কলোনি তৈরির দার্শনিক উত্তর। তাঁরা কলোনি তৈরি করেছে আমাদের সভ্য করতে, তাঁরা এটাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে আমরা চিন্তাহীন সত্তা। কার্ল মার্ক্সও বস্তু ও চিন্তার দ্বি বিভাগের বিরুদ্ধে, যদিও আজকের মার্ক্সবাদীরা মার্ক্সকে যান্ত্রিক বস্তুবাদী বানিয়ে ফেলেছেন। মার্ক্স যা নয় সেটাই তার উপরে মার্ক্সবাদের নামে আরোপ করা হয়েছে।
বস্তু ও চিন্তার এই দেকার্তিয় শাশ্বত পার্থক্য স্পিনোজা স্বীকার করেননি। একারনেই তিনি দেকার্তের থেকে পৃথক। তিনি তাঁর এই চিন্তাকে যেইসব প্রশ্ন তুলে দাড় করিয়েছেন তাতেই দেকার্তের চিন্তার ভীত নড়বরে হয়ে গেছে। তাই তিনি বিপ্লবী রাজনীতির কাছে অতি প্রাসঙ্গিক। কারণ পুঁজিবাদকে অতিক্রম করে যেতে হলে তো তার দার্শনিক ভিত্তিকেও আঘাত করতে হবে।
স্পিনোজা ঈশ্বর আর তার সৃষ্টিকে সমার্থক করে ভেবেছেন। স্পিনোজার ভাবনায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা আছে।
১/ সাবস্ট্যান্স
২/ অ্যাট্রিবিউট
৩/ মৌড
মৌড হচ্ছে সাময়িকভাবে বাস্তব গ্রহণ করে এমন কোন বিশেষ বস্তু বা ঘটনা, কোন বিশেষ রূপ বা আকৃতি।
আর আট্রিবিউট হচ্ছে, বুদ্ধি সাবস্ট্যান্সকে কীভাবে এসেন্স বা সারবস্তু হিসেবে পারসিভ করে যাকে আমরা সাধারনভাবে গুণ বলতে পারি।
আর স্যাবট্যান্স কী? স্যাবট্যান্সকে বুৎপত্তি গত ভাবে আমরা মনে করতে পারি, সেটা হচ্ছে তাই যা বস্তুর ভেতরে থাকে। স্যাবট্যান্স শব্দটা স্পিনোজা নিয়েছিলেন স্কলাস্টিকদের কাছে থেকে। স্কলাস্টিকেরা ব্যবহার করতেন OUSIA এটার মানে হচ্ছে “হওয়া”।
দেকার্ত এই পরিভাষাগুলোকে এভাবেই ব্যবহার করেছিলেন। “substance” হচ্ছে সেই পরম বস্তু স্বতন্ত্র সত্তা “Attribute” হচ্ছে সাবাস্ট্যান্সের অপরিবর্তনিয় ফিচার আর “Mode” হচ্ছে সাবস্ট্যান্সের পরিবর্তনশীল গুণ।
স্পিনোজা সাবস্ট্যান্সকে প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম করে কল্পনা করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃতি ঈশ্বর হয়ে ওঠে তার অন্তর্বর্তি তাড়নায়। একটা জিনিস স্পিনোজা নিজেই সতর্ক করে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে স্পিনোজার উদ্দেশ্য ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে অভিন্ন প্রতিপন্ন করা নয়। বরং ঈশ্বরের ইচ্ছাই প্রাকৃতিক নিয়ম, কারণ ঈশ্বর সমস্ত বস্তুর অন্তর্বর্তি কারণ। “প্রকৃতিই স্পিনোজার ঈশ্বর” এমন একটা ধারণা চালু হয়েছে সম্ভবত আইনস্টাইনের একটা উক্তি থেকে, এই ধারনাটা ভ্রান্ত। বরং স্পিনোজার ঈশ্বরের ধারণা ইসলামের তৌহিদের ধারণার কাছাকাছি।
স্পিনোজা বলেছেন মন যেমন জড় ধর্মী নয় বস্তুও তেমন মনো ধর্মি নয়। মস্তিস্কের ক্রিয়া যেমন চিন্তার কারণ কিংবা পরিনাম নয়, তেমনি দুটো ক্রিয়া স্বতন্ত্র বা সমান্তরালও নয়। কেননা দুরকম ক্রিয়াও নেই, দুরকম সত্তাও নেই। ক্রিয়া একটাই, ভেতর থেকে দেখলে চিন্তা, আর বাইরে থেকে দেখলে গতি। সত্তাও একটা, ভেতর থেকে দেখলে মন আর বাইরে থেকে দেখলে বস্তু, কিন্তু বাস্তবে এ হল দুয়েরই সমন্বয় বা যৌগিক মিশ্রণ। মন ও দেহ একে অন্যের উপর ক্রিয়া করেনা, কারণ তাঁরা আলাদা আলাদা জিনিস নয় তাঁরা অভিন্ন। দেহ মনকে চিন্তা করার কথা বলতে পারেনা, মন পারেনা দেহকে স্থির বা গতিশীল হওয়ার নির্দেশ। কারণটা এই যে মনের ইচ্ছা আর দেহের সংকল্প একই জিনিস।
স্পিনোজা এভাবেই দেহ ও মনের পার্থক্যকে ঘুচিয়ে দিয়েছেন। এভাবেই পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়েছেন বুদ্ধি এবং ইচ্ছার। সেটা না হয় আরেকদিন আলাপ করা যাবে।